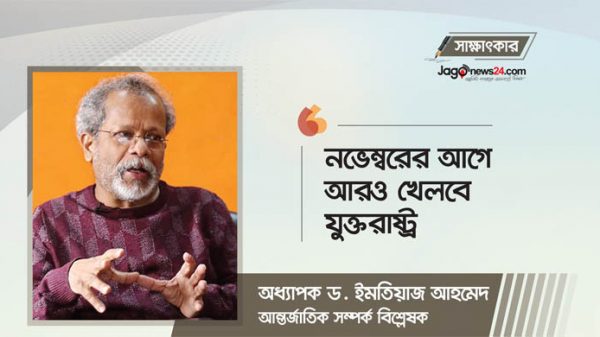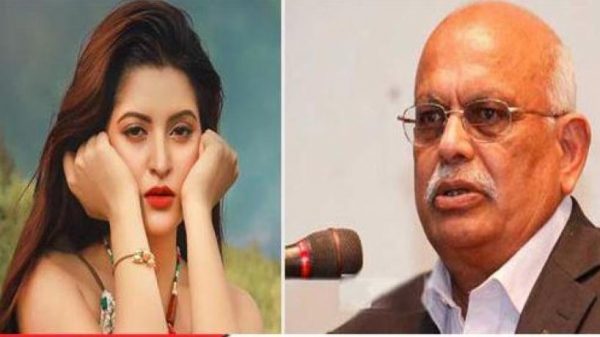শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রচেষ্টা ও বাস্তবতা
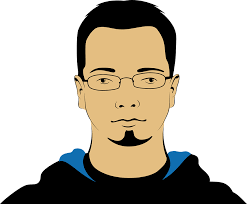
- আপডেট টাইম : বুধবার, ২১ আগস্ট, ২০১৯
- ৪৪৫ বার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
শস্য উৎপাদনের মতোই জ্ঞানও শ্রমেরই ফসল। বিদ্যালয়ে জ্ঞানের চর্চা হয়, সেখানে দুটি পক্ষ থাকে; শিক্ষক এবং ছাত্র। এদের মিলিত শ্রমেই শিক্ষার অনুশীলন। শিক্ষার মান সরাসরি নির্ভর করে শিক্ষকের মানের ওপর। শিক্ষকও একজন কর্মী। তিনি জ্ঞান আহরণ করেন এবং বিতরণ করেন। কিন্তু শিক্ষক কেবল যে দাতা তা নন, তিনি গ্রহীতাও। ছাত্রের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেন আগ্রহ ও প্রাণবন্ততা। ছাত্র আগ্রহী হলে শিক্ষকের আগ্রহ বাড়ে; ছাত্রের কৌতূহল, উচ্ছলতা শিক্ষককে প্রাণবন্ত করে তোলে। ছাত্রের প্রশ্ন ও কৌতূহল শিক্ষককে পাঠদানের বিষয়কে আরও ভালোভাবে জানার ব্যাপারে উৎসাহী করে। শিক্ষকতার কাজটা তখন জীবিকার্জনের একঘেয়ে গ্লানিকর কর্তব্য থাকে না। শিক্ষক চরিতার্থতা পান; যে চরিতার্থতা শিক্ষাদানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। ভালো শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে বেতন-ভাতার তুলনায় এই চরিতার্থতা কম মূল্যবান নয়। ভালো শিক্ষক না পেলে তো শিক্ষার গুণ ও মান বাড়বে না। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষক পাওয়াটা এখন বড় একটা সমস্যা।
মেধাবানদের শিক্ষকতায় নিয়ে আসা চাই। মেধাবান হওয়া অর্থ কেবল যে জ্ঞানী হওয়া, তা নয়; শিক্ষকতায় আগ্রহী হওয়াও চাই। অন্য চাকরি পাননি বলে শিক্ষক হয়েছেন- এমন লোকদের দিয়ে কুলাবে না। তেমন শিক্ষক চাই, যিনি জ্ঞানী, একই সঙ্গে উৎসাহী সেই জ্ঞানকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে এবং পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। এ রকম মানুষদের শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে আনতে হলে বেতন-ভাতার বিষয়টি দেখতে হবে বৈকি। বেতন-ভাতা সম্মানজনক হওয়া চাই এবং অন্য পেশার চেয়ে বেশি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, যাতে মেধাবীরা আসেন এবং কোচিং সেন্টারে না গিয়ে ক্লাসরুমে শিক্ষাদানেই নিবিষ্টচিত্ত হন। কিন্তু শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র ও উন্নত বেতন স্কেল তো বাস্তবে নেই। আর তার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ আনুপাতিক হারে বাড়ছে না। জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশের ওপরে সেটা কিছুতেই ওঠে না, ভীষণ তার গড়িমসি। জিডিপির ২ শতাংশ বরাদ্দ করলে কিছুই চলবে না, অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দ চাই। অনুৎপাদক ও আমলাতান্ত্রিক খাতগুলো থেকে টাকা কেটে সেটা নিয়ে আসা চাই শিক্ষায়।
কিন্তু সমস্যাটা কেবল বরাদ্দের নয়; বরাদ্দের যথাযথ খরচেরও। টাকা কেবল ঢাললেই চলবে না, দেখতে হবে ঠিক জায়গাতে গিয়ে পড়ছে কি-না। দুর্নীতি কত যে ব্যাপক, সে তো আমরা জানি। পুলিশের ডিআইজি যখন স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালককে ৫০ লাখ টাকা নগদ ঘুষ দেয়, তখন তো বোঝাই যায়, নজরদারিটা কত দুর্বল। আর ফাঁস হয়ে যাওয়া এ খবরের তাৎপর্যও উপেক্ষণীয় নয় যে, একজন শিক্ষা কর্মকর্তা ওই দুর্নীতি দমন কমিশনেরই একজন কর্মকর্তার সঙ্গে ঘুষের অঙ্কটিকে এক কোটি থেকে ৫০ লাখে নামিয়ে আনা যায় কি-না, এ নিয়ে দর কষাকষি করছেন। অন্য ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষাক্ষেত্র দুষ্ট হওয়ার পরে এখন নষ্ট হওয়ার পথে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, এটা আমরা জানি। আর এটাও জানি, বাধ্য হই জানতে যে, শিক্ষক হতে হলে নগদ টাকা ঘুষ দিতে হয়। আর সে টাকা যে সামান্য তা নয়, বিপুল পরিমাণেরই। নজরদারি তাই অত্যাবশ্যক। তার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সামাজিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের এগিয়ে আসা চাই। সমাজে সৎ লোক যে নেই, তা নয়। সংখ্যায় তারাই অধিক, কিন্তু তাদের ক্ষমতা নেই। কারণ তারা বিচ্ছিন্ন। অন্য ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সৎ মানুষদের ঐক্য চাই। আবার শুধু যে সরকারি বরাদ্দেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলবে, এমনও নয়। বেসরকারি দান-অনুদানও আসতে হবে। কিছু কিছু আসেও; আরও আসবে যদি আবহাওয়া তৈরি করা যায়। আবহাওয়া এখন বিরূপ। প্রকৃতিরও, সমাজেরও।
বিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকের মিলনকেন্দ্র ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু। বিদ্যালয় হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠান; যেখানে বিদ্যার চর্চা হয় সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবেও। সামাজিকতাটাই প্রধান। একজন শিক্ষার্থী যখন বাড়ি থেকে বিদ্যায়তনে আসে, তখন ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় তার প্রবেশ ঘটে। জায়গাটা মুক্তির। শিক্ষার্থীর জন্য একেবারে প্রথম শিক্ষাটাই হলো সামাজিকতার। এই শিক্ষা তার বাকি জীবনের জন্য হবে সবচেয়ে বড় সংগ্রহ। পরে তার জ্ঞান বাড়বে; বাড়বে তার সামাজিকতাও। সামাজিকতাটা বিঘ্নিত হয় যদি সে আনন্দ না পায়। যদি মনে করে সে মুক্ত প্রাঙ্গণে আসেনি, এসে পড়েছে কয়েদখানায় কিংবা কারখানায়; সে ক্ষেত্রে তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা যাবে সংকুচিত হয়ে।

এখন ওই সংকোচনটা বড় বেশি ঘটছে। শিক্ষা যা দেওয়া হচ্ছে সেটা পর্যাপ্ত নয়। আর যেটুকুই বা দেওয়া হচ্ছে তাও শিক্ষার্থী ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। তার সার্বক্ষণিক ভয় পরীক্ষার। আমাদের বিদ্যায়তনিক শিক্ষা সব সময় ছিল পরীক্ষামুখী। এখন সেটা রীতিমতো পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পড়ানো যা হচ্ছে তা পরীক্ষায় পাসের জন্য। পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং চেষ্টা হয়েছিল একেবারে প্রাথমিক স্তরেই পরীক্ষার হলে শিশুদের টেনে আনার। আশা করি, সেটা পরিত্যক্ত হবে। পরীক্ষা যত কম হয় ততই মঙ্গল, বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা। পরীক্ষার ব্যাপারে চাপ যত বাড়ে, মূল বই পড়ার প্রয়োজন তত কমে যায়। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর রপ্ত করতে ব্যস্ত থাকে, শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দিয়ে। শিক্ষকরাও ওইভাবেই পড়ান। ছাত্রদেরকে ভালো নম্বর পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করাটাই শিক্ষক হিসেবে তাদের সাফল্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিরিখ হয়ে দাঁড়ায়। আর পরীক্ষায় যে এমসিকিউ প্রশ্নরীতি চালু হয়েছে, এটা খুবই ক্ষতিকর। এতে শিক্ষার্থীরা এমনকি প্রশ্নটাও ভালো করে বুঝতে চায় না। এ বি সি ডি-তে দাগ দেওয়ার কায়দা শেখে। আরেক উৎপাত সৃজনশীল পদ্ধতি। এটা শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক কেউই ঠিকমতো বোঝেন না। ছাত্ররা তো বটেই, শিক্ষকরাও গাইড বুকের শরণাপন্ন হন। পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা, এমসিকিউ, সৃজনশীল পদ্ধতি- সবকিছুই একত্র হয় কোচিং সেন্টার ও গাইড বুক ব্যবসাকে সরগরম করতে।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার কথা ধরা যাক। সবাই বলেন, শিক্ষার মান এখানে বেশ ভালোভাবেই নেমে গেছে। বাড়িয়েই বলেন।কারণ মান যে অতীতে খুব উঁচু ছিল আর এখনও যে একেবারে অধঃপতিত, তা নয়। আসলে যা কমেছে তা হলো শিক্ষার্থীদের আগ্রহ। শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় কম আগ্রহী। তারা আসে, থাকে, চলে যায়; কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রবল আগ্রহ দেখা যায় না। এর কারণ আছে। মূল কারণটা ভবিষ্যৎ দেখতে না পাওয়া। অধিকাংশের চোখেই স্বপ্ন নেই, মুছে গেছে। যাদের আছে তাদেরটাও ম্রিয়মাণ। শিক্ষার্থীরা জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা দেখতে পায় না। এই অনিশ্চয়তা আগের দিনেও ছিল; কিন্তু তখন তবু আশা করা যেত যে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। এখন সে আশাটা ক্ষীণ। দেশে যে উন্নতি হয়েছে তার দুর্বলতাগুলোর মধ্যে খুব বড়মাপের একটি হলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাওয়া। উন্নতি যা হয়েছে তার প্রায় সবটাই শ্রমের কারণেই; কিন্তু বিনিয়োগ ঘটছে না। কর্মের বিপুল শক্তি আটকা পড়ে গেছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জাঁতাকলে। বেকারত্বের সমস্যাটা ক্রমাগত বাড়ছেই; বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা তো এখন ভয়াবহ। যে তরুণ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে; তার দুশ্চিন্তা হয়, বের হয়ে কী করবে। পড়ালেখায় তার সেই দুর্দান্ত আকর্ষণটা নেই, যেটা থাকা আবশ্যক ছিল। ছাত্রের এই অনাগ্রহ শিক্ষককে নীরবে পীড়িত করে; জ্ঞানের অনুশীলনটায় প্রাণের ঘাটতি ঘটে যায়।
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা আসলে খুবই বড় ব্যাপার। আগ্রহের অভাব ঘটলে গ্রহণক্ষমতা হ্রাস পায়। হ্রাসপ্রাপ্তির অবশ্য আরও কারণ আছে। সেগুলোর একটা হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক জীবনের স্তিমিত দশা। শিক্ষার অনুশীলন কেবল ক্লাসে, লাইব্রেরিতে ও ল্যাবরেটরিতেই চলে না। ঘটে ছাত্রাবাসে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, পরস্পরের মেলামেশায় এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। এটা অবশ্যই তাৎপর্যহীন নয় যে, বিগত ২৮ বছর ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনটা পরাধীনতার আমলে কখনও ঘটেনি; না ব্রিটিশ শাসনে, না পাকিস্তানি শাসনে। এটা সার্বিক ব্যবস্থারই একটি প্রতিফলন। বোঝা যাচ্ছে, প্রচারকার্য যতই চলুক, সারবস্তুতে গণতন্ত্র আসেনি। ছাত্র সংসদ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রাণবন্ততার কেবল ধারক এবং বাহকই নয়; প্রধান উদ্যোক্তাও। ছাত্র সংসদের নির্বাচন শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসব, মেধাবানদের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি লাভের সুযোগ এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে সজীব রাখার কর্মাধ্যক্ষ। শিক্ষাঙ্গন যদি আলোচনা, বিতর্ক, নাটক, গান, সাহিত্য সৃষ্টি, খেলাধুলা, জ্ঞানীদের বক্তৃতায় মুখরিত না থাকে; তাহলে তো শিক্ষাঙ্গন তার প্রাণই হারিয়ে ফেলে। দেখা দেয় আবিলতা। ছেলেমেয়েরা টের পায় যে সুস্থ বিনোদন নেই, আদান-প্রদান নেই চিন্তার ও কল্পনার, অনুশীলন নেই সাংস্কৃতিক মেধার, বিকাশ নেই নেতৃত্বদানের শক্তির। তারা হতাশ হয়, অবসাদে ভোগে, মাদক ধরে কেউ কেউ; অন্যরা ঝিমায়, দেখা দেয় কলহ-বিবাদ। আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। আর অতীতে যা কখনও শোনা যায়নি তা এখন শোনা যায়। সেটি হচ্ছে যৌন হয়রানি। চরম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘটনায়, যেখানে তথাকথিত এক ছাত্র ধর্ষণের শতসংখ্যা পূর্তির ঘোষণা দিয়েছিল। যৌন হয়রানির অভিযোগ কেবল ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদের ব্যাপারেও উঠছে। সোনাগাজীতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ যখন ছাত্রীকে হয়রানি করে এবং ছাত্রী তার প্রতিবাদ জানালে অধ্যক্ষটি যখন তার রাজনৈতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে জীবন্ত অবস্থায় ছাত্রীকে পুড়িয়ে মারে, তখন একটি চরম বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষায়তনে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার বাস্তবতাটা যে কত দূর প্রসারিত হয়েছে, সেই সত্যটাই বের হয়ে আসে।
শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্নেষক