হিজলপুরাণ ও আমাদের সমৃদ্ধির গল্প
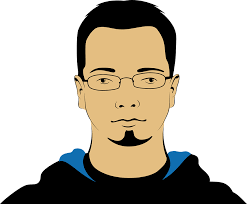
- আপডেট টাইম : শুক্রবার, ৩১ আগস্ট, ২০১৮
- ১২১৬ বার

–মুহাম্মদ শাহজাহান
শৈশবের কথা দিয়েই শুরু করি। মাঝে মধ্যে আমরা ছোটরা মিলে সন্ধ্যের পর ছিলক বলায় মেতে উঠতাম। আমাদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হত কে কত ছিলক বলতে পারে; আর কে কত ছিলকের সঠিক উত্তর দিতে পারে। সে সব ছিলক বলার আসরে ধীরে ধীরে শিশুদের সংখ্যাটা যেমন বাড়ত, তেমনই এই আসরটাও জমে উঠত আর চলত ঘন্টার পর ঘন্টা। তখন আমাদের মুখ থেকে কত কত শ্রুতিমধুর ছিলক যে নির্গত হত, তার অনেক কিছুই এখন আর মনে পড়ে না। তবে সেসব আসরে প্রায় সময়ই একটি ছিলক অবশ্যই বলা হত-
‘ইজলের ঝড়ি-মরি পিতলের ছানি,
কোন দেশে দেইখা আইলাম গাছের আগায় পানি?’
বর্ণিত ছিলকটা আসলে কঠিন নয়; বলা যায় সহজ ছিলক।পাঠকও একটু ভাবলে এর সঠিক উত্তর আশা করি পেয়ে যাবেন।
এক.
হিজল- স্থানীয়ভাবে ‘ইজল’ নামে পরিচিত। ভাটিবাংলার সুপরিচিত মাঝারি আকারের চিরসবুজ দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ; কাণ্ড- অমসৃণ, বাকল ঘন ছাই রঙের ও পুরু। চারদিকে বিস্তৃত ডালপালা নিয়ে গাছটি ১০ থেকে ১৫মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বাংলার কোথাও হিজল, নদীক্রান্ত, জলন্ত নামে পরিচিত; সংস্কৃত নাম- নিচুল। ভাটি অঞ্চলের আরেকটি সুপরিচিত গাছ করচ, তার মতই দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে; বিশেষ করে বর্ষাকালের পাঁচ/ছয় মাস পানিতে তলিয়ে থেকেও দিব্যি বেঁচে থাকে। জলাবদ্ধ এলাকা বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলের খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর-বাওর ও ডোবার ধারে সর্বত্র চোখে পড়ে হিজল-করচের যুগলবন্ধি অবস্থান।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হিজল গাছে ফুল ফোটে।১০-১২সি.মি. দৈর্ঘ্যরে ঝুলন্ত পুষ্পদন্ড; যার মধ্যে জড়াজড়ি করে লেগে থাকে অসংখ্য গোলাপি রঙের ছোট ছোট ফুল। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটা শুরু হয়; ভোরে সূর্যের আলোয় ধীরে ধীরে ঝরে পরে। সকালে হিজলতলায় গেলে মনে হবে গোলাপি একখান বিছানা পাতা; পানির ওপর ঝরে পড়া ফুলের অপূর্ব আস্তরণ। গ্রামের শিশুরা সে ফুল কুড়িয়ে তৈরী করে নিজেদের পছন্দমত এক একটা ফুলের মালা।হিজলের ফুলে থাকে এক ধরনের মিষ্টি মাদকতাময় গন্ধ; রাতে বা ভোরে হিজল তলার পাশ দিয়ে গেলে মিষ্টি ঐ ঘ্রাণ আচড়ে পড়ে সবার নাকে-মুখে। হিজলের ফুলে মুগ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই লিখেছেন-
‘পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকন কালা ।’
নির্জনতা প্রিয় রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ।বাংলার চিরায়ত রূপ বর্ণনায় হিজলও ওঠে এসেছে তাঁর কবিতায়-
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব’সে আছে
ভোরের দুয়েলপাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশথেরা ক’রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে!
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ……
হিজল ও তার ফুলের সৌন্দর্য্য কেবল আধুনিক কাব্য-সাহিত্যেই নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যেও পাওয়া যায়।মঙ্গলকাব্য ও বিভিন্ন গীতিকায় হিজলগাছের উল্লেখ রয়েছে।সিলেটের পুথিগ্রন্থে কিংবা শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় দ্বিজ কানাই প্রণীত ‘মহুয়া পালা’য় হিজল গাছ প্রসঙ্গটি এভাবে উঠে এসেছে-
‘পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া বসিল শিওরে।
নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে।’
হিজল গাছের তলায় সুমিষ্ট বাতাস বহে- এ রকম একটি ধারণা গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।দ্বিজ কানাই হয়ত বা সেটা বুঝাতেই এখানে হিজল গাছের কথা বর্ণনা করেছেন।এছাড়া নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত ‘চন্দ্রাবতীর পালা’র নায়ক জয়চন্দ্র তার প্রেমিকাকে মনের কথা জানাতে পত্র লিখেন-
‘লিখিয়া রাখিল পত্র ইজল গাছের মূলে
এইখানে পড়বি কন্যা নয়ন ফিরাইলে।
সাক্ষী হইও ইজল গাছ নদীর কূলে বাসা
তোমার কাছে কইয়া গেলাম মনের যত আশা।’
এত গেল কাব্য-সাহিত্যে হিজল ও তার গোলাপী ফুলের নান্দনিক ব্যবহার। হিজল গাছের আরেকটি বিশেষ ব্যবহার, সেটা হলো হিজল-করচ গাছের তৈরী প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল। ভাটিবাংলার হাওরপারে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোও দেখা মিলে প্রচুর হিজল-করচের গাছ; সেগুলো অবশ্য এমনি এমনি বেড়ে ওঠেনি। গ্রামবাসী কৃষকেরা বর্ষা মৌসুমে হাওরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে বসতবাড়ির ভিটে-মাটিকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদে, পরিকল্পিতভাবে বাড়ির চর্তুদিকে লাগিয়ে দেন এসব হিজল-করচের গাছ।সেগুলোই দিন দিন বেড়ে ওঠে, এক সময় রূপ নেয় প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল হিসেবে।
প্রকৃতির সন্তান মানুষ; সে বিভিন্নভাবে আশ্রয় খোঁজে, নিরাপত্তা খোঁজে প্রকৃতির কাছে। মানুষ যত প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে- ভাল থাকে, সুস্থ থাকে, প্রাণবন্ত থাকে। আবার কখনও এই প্রকৃতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় মানুষকে; সেটা অবশ্য তার ঠিকে থাকার তাগিদে।প্রকৃতির আরেক অবিচ্ছেদ্য অংশ গাছ-গাছালি; সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ কতভাবে যে তার থেকে সুবিধা নিয়ে আসছে এবং আজও কতভাবে যে তার ওপর নির্ভরশীল সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।বেঁচে থাকার জন্য চাই অক্সিজেন, খাদ্য, বাসস্থান; এসব কিছুর জন্য শুধু মানুষই না প্রাণী জগতের সবাই গাছ-বৃক্ষের উপরই নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত গাছ-গাছালিই মানুষের অকৃত্রিম প্রকৃত পরম বন্ধু হিসেবে পরিচিত; সে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে আছে প্রাণী জগতের বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষকে।সেই গাছ-বৃক্ষ প্রজাতির একটি হিজলগাছ। এবার শুনি আমাদের সমৃদ্ধির গল্প; যার সাথে অতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে হিজলের নাম আর গুণে অলংকৃত একটি বাড়ি ‘হিজল’।
দুই.
একজন উচ্চপদস্থ সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা; সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে কর্মব্যস্ত তাঁর জীবন। দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান কর্মকর্তার ফুরসৎ নেই দু-দন্ড বিশ্রামের; তারপরও একটুখানি সুযোগ পেলে ছুটে আসেন অজপাড়াগাঁয়, তাঁর নিজ গ্রামে। শৈশব আর কৈশোরের কত সোনালী স্মৃতি জমে আছে তাঁর মনের গহীনে; এ গ্রামেই যে তাঁর জন্ম, আর বেড়ে ওঠা। হয়ত বা স্মৃতিকাতর কোনো মুহূর্তে কল্পনায় হারিয়ে যান হেমন্তের দিগন্ত বিস্তৃত সুবজ মাঠে; কিংবা ছায়া-সুনিবিড় হিজল-করচের বাগে। কখনও তাঁর কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে বিশাল সাংহাই হাওরের আদিগন্ত বিস্তৃত কৃষকের ধানক্ষেত। গাঢ় সবুজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লোকচুরি খেলা; মৃদুমন্দ বাতাসে আপন মনে নেচে ওঠা ধানের শিষের ঢেউ খেলানো হাসি। কখনও দৃষ্টি তাঁর আটকা পড়ে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের ভেলায়।
আবার কখনও তাঁর মানসপটে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সাংহাই হাওর ও তার পারে গড়ে ওঠা গ্রামের বর্ষার চিরচেনা অন্য রূপ; সেখানে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মৌসুমী বাতাসে অশান্ত হাওরে বিশাল বিশাল ঢেউয়ের নাচন; কখনও তার শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ, বিল-ঝিল ছেয়ে আছে শাপলা-শালুক আর নাম না জানা জ্লজ উদ্ভিদে। বসত বাড়ির সামনে প্রবাহিত ছোট নদী বাউরি। কখনও নিজেকে দেখতে পান টিনসেড বাংলো ঘরের বারান্দায়; বসে আছেন কাঠের তৈরি ইজি চেয়ারে। দৃষ্টি বর্ষার পানিতে পরিপুষ্ট নদীর বুকে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেন নদীর বুক ছিড়ে ছুটে চলা গ্রামবাসী কৃষকের শত কাজে ব্যবহৃত ছোট ছোট নৌকার আনাগুনা। কখনও আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের আফালে নিজেকে খুঁজে ফিরেন পানিবন্দি দ্বীপের মতো গ্রামের ছোট্র একটি টিনের ঘরে; কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন টিনের চালে অবিরাম বৃষ্টি পড়ার ঘোর লাগা টাপুর-টুপুর শব্দ।
যেমন প্রকৃতিপ্রেমী, তেমনি পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ ও মেধাবী এক জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক কর্মতৎপরতা; যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। এমনি কঠিন দায়িত্ব আর স্বপ্ন নিয়ে ছুটে বেড়ান দেশের আনাচে-কানাচে; প্রত্যক্ষ করেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা।যেখানে আজও উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণের দীর্ঘ ২৫বছর; যে সময়টুকুতে বলতে গেলে বাংলার কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি পাকিস্তান সরকার। পরিণতিতে বাংলার জনগণের কাংখিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ; সে সময় হানাদারদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ আর ধংসলীলার হাত থেকে রেহাই পায়নি বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোও।তাঁর নিজ গ্রামেও ঘটে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ আর ধংসলীলা; কল্পনায় ভেসে ওঠে গ্রামে বসবাসকারী কৃষকদের আর্থ-সামজিক অবস্থার করুণ প্রতিচ্ছবি।দায়িত্ব, কর্তব্য, ভাললাগা, হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন, অন্যদিকে শেকড়ের টান মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তাঁর রক্তে।তাঁর হৃদয়ে জন্ম নেয় এক মহান স্বপ্ন; অবহেলিত পশ্চাৎপদ ভাটিবাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।
সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপদানে নিরবে নিভৃতে, পশ্চাৎপদ অবহেলিত ভাটিবাংলার উন্নয়নে মনোযোগী ও তৎপর হয়ে ওঠছিলেন ডুংরিয়া গ্রামের কৃতিসন্তান; এক সময়কার বাংলাদেশ সরকারের জেলা প্রশাসক (ডিসি) এম. এ. মান্নান। তাঁরই ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায়- প্রবাসীদের সুবিধার্থে ১৯৮৭ সালে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন সময়ের দেশ-বিদেশের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম পোস্ট অফিস। পাশাপশি তিনি উদ্দ্যোগ নেন শান্তিগঞ্জ-ডুংরিয়া রাস্তা আরো উঁচু, প্রশস্থ ও পাকা করণের। গ্রামের অধিকাংশ নিচু পায়ে চলা পথগুলো, যা বর্ষাকালের ছয়মাস পানির নিচে ডুবে থাকত, সেগুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে উচু রাস্তায়; একসময় রূপান্তরিত হয় পাকা সড়কে। বর্ষাকালে পানি নিস্কাশন ও যাতায়াতের সুবির্ধাতে গ্রামে নির্মিত হয় কয়েকটি ব্রীজ-কার্লভার্ট। এক সময়কার শান্তিগঞ্জ-ডুংরিয়া রাস্তা বিস্তৃতি লাভ করে শান্তিগঞ্জ-রজনীগঞ্জ সড়কে; যে সড়কে দিন দিন বাড়ছে যানবাহনের ছুটে চলা; তেমনি দেশের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে গ্রাম ডুংরিয়া।
হাওরপারের অবহেলিত পশ্চাৎপদ গ্রামবাসীর জন্য তিনি নিয়ে আসেন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিক্ষার আলো; উন্নত-সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল ভবিৎষ্যতের স্বপ্ন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্ঠায় ১৯৮৭ সালে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ডুংরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়; যা ২০১৭ সালে উন্নীত হয়েছে ‘ডুংরিয়া হাই স্কুল এন্ড কলেজে’। নব্বই দশকের শুরুতে ১৯৯০ সালে তাঁর উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় গ্রামে আসে বিদ্যুৎ; প্রান্তিক কৃষকের সুবিধার্থে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা পায় ‘বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক’ ডুংরিয়া শাখা। গ্রামবাসীর বিশুদ্ধ পানীয়-জলের তীব্র সমস্যা; তা সমাধানে নব্বই দশকের প্রথমার্ধেই তাঁর প্রচেষ্টায় গ্রামে স্থাপিত হয় বেশ কিছু নলকূপ।
এলাকার একটি বড় গ্রাম ডুংরিয়া। গ্রামে একটি মাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; গ্রামের কয়েকটি পাড়া/মহল্লা থেকে বিদ্যালয়টির অবস্থান বেশ দূরে, বিশেষ করে বর্ষাকালে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়াটা ছিল অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শিশুদের আসা-যাওয়া নির্বিঘ্ন করতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের হার বাড়াতে তিনি ১৯৯২ সালে গ্রামে নির্মাণ করেন আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ডুংরিয়া উত্তর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। নিজ গ্রামে এমনি কতশত উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অবদান লিখে শেষ করার নয়; এখনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলছে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কার্যক্রম।
আজকের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্র শান্তিগঞ্জ। দিন দিন তার বিস্তৃতি বেড়েই চলছে। আজকের উপজেলা ভিত্তিক এতসব মহাকর্মযজ্ঞের পিছনে যার বিশেষ অবদান তিনি হলেন ডুংরিয়া গ্রামের সেই কৃতিসন্তান, এক সময়কার জেলা প্রশাসক, পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক (ডিজি), নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিবসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে সফলভাবে দায়িত্ব পালনকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এম. এ. মান্নান, এমপি; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী।
মহান স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে এখন প্রজ্জ্বলিত আলোর মশাল। যার আলোয় আলোকিত হচ্ছে এক সময়কার অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম ডুংরিয়া; দ্রুতগতিতে দূর হচ্ছে এখান থেকে কুশিক্ষা আর অশিক্ষা। তেমনি সে আলো তার নিজস্ব গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে হাওর বেষ্ঠিত অবহেলিত জনপদ সুনামগঞ্জ জেলার সর্বত্র। জেলার সর্বত্র লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্ঠায় বিশেষ করে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুত গতিতে গড়ে উঠছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, ব্রীজ, কার্লভার্ট ইত্যাদি।
ভাটিবাংলার প্রান্তিক অবহিলেত জনগোষ্ঠী আজ স্বপ্নে বিভোর, স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পর তারা স্বপ্ন দেখছেন; খুঁজে পেয়েছেন তাদের এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টাকে। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সরকারি ভাবে গৃহিত হয়েছে; এখন অপেক্ষা শুধু বাস্তবায়নের। দক্ষিণ সুনামগঞ্জ তথা সুনামগঞ্জ জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের চিত্রটা এখন এমনই; তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় যার পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
আজ দেখতে পাচ্ছি পরিচ্ছন্ন রাজনীতির চর্চা, সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনার ঠিকানা যেমন একটা, তেমনই গাঁও-গেরামের অবহেলিত মেহনতি জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দূর্দশা, তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলা, শুনা এবং সেসব সমস্যা সমাধানের ঠিকানাও একটা; সেটা হলো সবার সুপরিচিত বাড়ি- ‘হিজল’।
লেখক: ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ।
৩০.০৮.২০১৮খ্রি:













